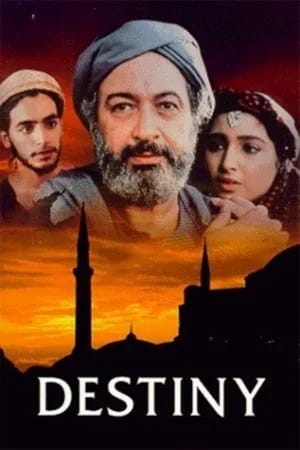যারা চিন্তাশীল আছেন, চিন্তা করেন তারা কখন টের পান যে তারা চিন্তাশীল? যখন তারা নিজেরা বুঝেন একটা, কিন্তু দেখতে পান ঘটতেছে আরেকটা। তখন তাদের নিজেদের বুঝ এবং দেখতে থাকা ঘটনার একটা সংঘর্ষ হয়, একটা কন্ট্রাডিকশনের যাতনা তিনি অনুভব করতে থাকেন। প্রতিটা চিন্তাশীল লোকের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর পরে তার ভেতরে সন্দেহের শুরু হয়, তার অনুসন্ধান শুরু হয়।
চিন্তাশীলের সাথে সমাজের প্রথা, নীতি, ধারণার যে ক্ল্যাশ, এটা প্রায় সকল সময়ের চিন্তকের লেখায় কমবেশী পাবেন। সমাজের রীতি প্রথা ধারণায় আবদ্ধ না থেকে ব্যক্তি হিশাবে নিজে চিন্তা করার গুরুত্ব সকল সময়ের চিন্তকেরাই তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, মানুষের মধ্যে কীভাবে রিজন বা চিন্তার সূত্রপাত হয়, কীভাবে একজন লোক চিন্তক বা দার্শনিকে পরিণত হয়, এই বিষয়ে জ্ঞানীরা ভেবেছেন।
মানুষের মধ্যে কি জন্ম থেকেই চিন্তা বা রিজন থাকে, নাকি সে জন্মের পরে অনুসন্ধিৎসু ভাবে নানা কিছু দেখে, এক্সপেরিয়েন্স করে, এবং এর মাধ্যমেই তার রিজন তথা বোধ বুদ্ধি তৈরি হয়?
এইসব বিষয় নিয়ে একটা দার্শনিক মেজর কাজ হচ্ছে আন্দালুসিয়ান দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের উপন্যাস, হাই ইবনে ইয়াকদান (বা ইয়াকজান)। ১২ শ শতকে এটি লেখা হয়।
দার্শনিকেরা তার সময়ের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন, ওই সময়ের চিন্তার সমস্যাগুলি সমাধান করতে যান। ইবনে তোফায়েলও এই বইতে কয়েকটা সমস্যার সমাধান করতে গেছিলেন বা ওই বিষয়ে তার চিন্তা উপস্থাপন করতে গেছিলেন। যেগুলা ওই সময়ের আন্দালুসিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের আলোচ্য বিষয় ছিল। এর প্রায় শতবছর আগে ছিলেন শক্তিশালী দার্শনিক ইবনে সিনা, তার চিন্তার প্রভাব ইবনে তোফায়েলের মধ্যে ছিল ব্যাপক ভাবে।
হাই ইবনে ইয়াকজানে ইবনে তোফায়েল সে সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে যান, এর মধ্যে গুরুতর কয়েকটি হলো,
মানুষের ভিতরে চিন্তা কীভাবে ডেভলাপ করে। কীভাবে একজন লোকের রিজন ডেভলাপ হয়, এবং সে দার্শনিক হয়।
একজন মানুষ কি তার আশপাশ থেকে দেখা, চিন্তা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজে নিজে চিন্তার বা আধ্যাত্মিক সত্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে।
নবীদের যে আলোকপ্রাপ্তি হয় ওহী বা বানীর মাধ্যমে, তারা যে সত্য জ্ঞান লাভ করেন, ওই সত্যে কী একজন ব্যক্তি নিজে নিজে চিন্তা করে পৌঁছাতে পারে।
দার্শনিক এইসব সমস্যা বিষয়ে তার বক্তব্য ইবনে তোফায়েল এলিগোরিক্যাল এই উপন্যাসের মাধ্যমে লিখেছেন। একইসাথে এটা যেমন দার্শনিক কাজ, তেমনি উপন্যাসের স্ট্র্যাকচারের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। যেই সময়ে লেখা হইছে ওই সময়ে, এবং এরপরে শত শত বছর মুসলিম ও পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজে প্রভাব রেখে গেছে।
ইবনে তোফায়েল তার উপন্যাসে দেখান এক নির্জন দ্বীপে এক ছেলে, হাই ইবনে ইয়াকজান একা মানুষ হচ্ছে, এক হরিণ তারে বড় করে।
ছেলেটি কীভাবে এই দ্বীপে এলো এই বিষয়ে তিনি আবার দুইটা গল্প বলেন। এক গল্প, এই দ্বীপটার প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন আদর্শ যে, এখানে এমনি থেকে শিশু জন্ম নিতে পারে। কীভাবে সেটি হতে পারে তার বর্ননা দেন দ্বীপের পরিবেশ বর্ণনা করে। এরিস্টটলিয়ান দার্শনিক ইবনে সিনা তাত্ত্বিক ভাবে মনে করতেন, আদর্শ পরিবেশে স্বতস্ফূর্ত ভাবে মানুষ জন্ম নেয়া সম্ভব।
দ্বিতীয় গল্প, পাশের এক রাজ্যে এক শক্তিশালী রাজার বোনের কোনোভাবে এক সন্তান হয়। স্ক্যান্ডাল এড়াতে তারা শিশুটিকে ভাসিয়ে দেয় একটা বাক্সে ভরে।
এই রকম, একই বিষয়ের একাধিক কারণ দেখানো, এবং কোনটাতেই পক্ষপাত না করা, পাঠকরে কয়েকটা ধারণা দেয় কেন এটা ঘটল। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছু বলে না। পরবর্তীকালের সাহিত্যে প্রচুর ব্যবহার হইছে এই ন্যারেটিভ স্টাইল, আধুনিক আন রিলায়েবল ন্যারেটর হচ্ছে এই স্টাইলের আরেক রূপ। জাপানি অসাধারণ গল্পকার রিউনোসুকে আকুতাগাওয়া তার বিখ্যাত ইন এ গ্রুভ গল্পে এর ব্যবহার আছে, যেটা থেকে জাপানি মাস্টার ফিল্ম মেকার আকিরা কুরোসাওয়া বানান রাশোমন ফিল্ম। আমার অনেক গল্পে এটা সরাসরি, বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার হয়। যেমন কতো শতো মুখ গল্পের সব গল্প, নিমাত্রা পীরছাব বইয়ের পাঁচটা গল্পের সম্মিলনে যে গল্প, এইগুলা এই স্টাইলের বর্ধিত রূপ। স্টাইল মুখ্য না অবশ্যই, মুখ্য হচ্ছে পাঠকরে একটা ফিল দেয়া বা মেসেজ দেয়া উপস্থাপনের ভঙ্গিমায়।
ইবনে তোফায়েল কেন এই দুইটা গল্প বললেন, কেন একটা বেছে নিলেন না? কারণ, তিনি চাইছেন প্রথমেই তার পাঠকরে গল্পের মেজাজ ধরাইয়া দিতে, সরাসরি উত্তরের চাইতে এখানে অনুসন্ধান থাকবে। অনুসন্ধানের পরে মিলবে গল্পের সত্য। যেমন, এই দুই গল্পের, বা হাই ইবনে ইয়াকজানের জন্ম বিত্তান্তের পরে আসে হরিণ। হরিণ তারে খুঁজে পায়, হয়ত সে সমুদ্র পারে নিজ থেকে জন্ম নিছে, অথবা ভেসে আসছে। হরিণ তারে বাঁচায় ও মাতৃমমতায় পালন করে, তার নিজের বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছিল এক ঈগল। এখান থেকেই গল্প সত্য ধারায় বইতে থাকে। অর্থাৎ, দুই ন্যারেটিভের যে সন্দেহটা লেখক তৈরি করছিলেন, হরিণ আসার পরে, তিনি দুইটারে এক করে মূল গল্পে চলে যান। সাহিত্যিক স্টাইল হিশেবে এটা দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত, এবং শৈল্পিক।
অথবা এর কারণ হতে পারে, তিনি তার মূল গল্পের সারমর্ম প্রথমেই বলে দিলেন হাই এর জন্ম বিষয়ে এই দুই ধরণের গল্প বলে। এক, মানুষের ভেতর স্বতস্ফূর্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তির ডেভলাপমেন্ট হতে পারে, দুই, যেটা বেশীরভাগ মানুষ মনে করে, কোন রূপক গল্পে তারা বিশ্বাস করে যে, এইভাবে বুদ্ধিবৃত্তির জন্ম হয়।
হাই ইবনে ইয়াকজানের জীবনের অনুসন্ধান শুরু হয়। সে প্রথমে পশুপাখির ভাষা শিখে, চারপাশ দেখে, আস্তে আস্তে বড় হয়। একসময়, ৭ বছর বয়েসে তার মাতৃসম হরিণ মারা যাবার দশায় উপস্থিত হয় । হাই দুঃখ পায়। এই প্রথম তার মৃত্যুর সাথে পরিচয়। সে এক পর্যায়ে হরিণকে বাঁচাতে গিয়ে তারে কেটেকুটে খুঁজতে থাকে কোন জায়গায় অসুস্থতা। হরিণকে সে বাঁচাতে পারল না, কিন্তু এই অনুসন্ধানে প্রাণীদের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে দেখতে পেল। আরও কিছু প্রাণী কাটাকাটি করে হাই বুঝার চেষ্টা করে দেহ কী, প্রাণ কী। সে বুঝতে পারে আসলে দেহের ভেতরের প্রবাহই মূল, বাকী শারীরিক বিষয় অনুষঙ্গ মাত্র।
এই কাটাকাটি এবং শারীরিক বিষয় বর্ণনায় ইবনে তোফায়েল গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের জ্ঞান ব্যবহার করেছেন, এবং তিনি নিজেও ছিলেন সফল চিকিৎসক।
হাই এর পোশাকের চেতনা হয়, সে নিজেরে নগ্ন বুঝতে পারে। ঈগলের পশম দিয়ে সে পোশাক বানায়। অন্যান্য প্রাণীদের উপর সে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করে, সে আগুন, লাঠি ইত্যাদির ব্যবহার শিখে ফেলে।
হাই এই সময়ে আরো গভীর অনুসন্ধানের দিকে ধাবিত হয়। এই সকল কিছু কী করে এলো বা এর সৃষ্টিকর্তা কে। সে দুইটা যুক্তি দেয়, এক, এই সকল কিছু আগে ছিল না, তৈরি হয়েছে অন্য কোন অবস্তুগত সত্তা (সৃষ্টিকর্তা) থেকে। যুক্তি দুই, এই সকল কিছু শুরু থেকেই ছিল, অনন্তকাল ধরে। কিন্তু অনন্তকাল ধরে কোন কিছু চলতে থাকলে, তার মধ্যে অনন্ত শক্তি উদ্ভবের সুযোগ থাকতে হবে, কিন্তু সেটা তো সম্ভব না, ফলে, হাই, তার যুক্তি এক এ ফিরে গেল। সে বুঝল একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।
এই যুক্তি ইবনে তোফায়েল বানিয়েছেন এমন না। এটা এরিস্টটলের যুক্তি, যা পরে ইবনে সিনা ব্যবহার করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে ইবনে তোফায়েল ১১ শতকের দার্শনিক ইবনে সিনা দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত ছিলেন, আগে উল্লেখ করেছি। হাই ইবনে ইয়াকজান নামে ইবনে সিনাও এক আধ্যাত্মিক গল্প লিখেছিলেন, কবিতার মত ছোট আকারে তিন পার্টে তিনি তার নিজের আধ্যাত্মিক ভ্রমণকে সাংকেতিক ভাষায় লিখেন হাই ইবনে ইয়াকজান, রিসালাত আল-তাইর, এবং সালামান ওয়া আবসাল নামে। ইবনে তোফায়েল যখন হাই ইবনে ইয়াকজান নামে উপন্যাস লিখেন, তার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন আলাদা ছিল, কিন্তু তিনি ইবনে সিনার লেখা থেকে নামগুলা নেন। আর নিজে নিজে স্বশিক্ষিত দার্শনিক হবার ধারণাটাও ইবনে সিনার, তিনি নিজেকে ঐরকম ভাবতেন তার আত্মজীবনীতে দেখা যায়।
হাই বুঝতে পারল একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। সে বুঝতে পারে তার শারীরিক অস্তিত্ব আসল না, তার আত্মা আছে, যা ওই সৃষ্টিকর্তার সাথে যুক্ত, কারণ আত্মাও অবস্তুগত। হাই বুঝতে পারে এর জন্যই সে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা, এবং তারে সেই সর্বোচ্চ উৎকৃষ্টতায় যাইতে হবে। তাই সে সমস্ত প্রাণীদের প্রতি যত্নশীল হয়ে পড়ে, যে অন্য প্রাণীদের খাওয়া ত্যাগ করে, গাছের যত্ন নিতে থাকে। সে প্রথমে কোন প্রাণ খাবে না ঠিক করে। কিন্তু দেখে এতে তার না খেয়ে থাকতে হবে ও সে মারা যাবে। তাই সে যেটুকু প্রয়োজন ওইটুকু শস্যাদি আহার করতে ঠিক করে।
তখন হাই এর ইকোলজিক্যাল থিংকিং ডেভ্লাপ হয়েছে। সে মনে করতে থাকা দুনিয়ার সকল কিছুরই প্রয়োজন আছে, কোন কিছুই নষ্ট করা যাবে না।
হাই এর সেই সর্বোচ্চ সত্ত্বা তথা সৃষ্টিকর্তাকে বুঝার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়, সে তার সাথে একাত্ম হবার তাড়না অনুভব করে।
সে এক গুহার মধ্যে সৃষ্টি কর্তার ধ্যান করতে থাকে, এবং দীর্ঘ ধ্যানের মাধ্যমে ৪২ বছর বয়েসে সে একসময় উপলব্ধি করে সে সৃষ্টিকর্তার সাথে মিশে যাচ্ছে। ইবনে তোফায়েল এই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি, কারণ এই অবস্থা ব্যক্তিকে নিজে এক্সপেরিয়েন্স করতে হয়, সে অন্যরে বলে বুঝাতে পারে না। এটা ইমাম গাঁজালির সূফিবাদের ড্রিম এনালজির লজিক, যেটা নিয়ে আমি আগে লিখেছিলাম। ইবনে তোফায়েল ইমাম গাঁজালি দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। তার হাই ইবনে ইয়াকজান ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়।

এই আধ্যাত্মিকতার স্তর রিজন বা যুক্তির স্তরের থেকে উপরের স্তর।
ইবনে তোফায়েল এরপর তার গল্পে ধর্মরে আনেন, এবং ধর্মের সাথে দার্শনিকের ও সূফীর যে কোন বিরোধ নাই, তা দেখাতে চান।
হাই যে দ্বীপে থাকত, তার পাশের এক দ্বীপে জনবসতি ছিল। ওইখানে একটা ধর্ম ছিল, কিন্তু মানুষেরা হয়ে পড়েছিল দূর্নীতিগ্রস্থ। ইবনে তোফায়েল ধর্মটার কোন নাম বলেন নাই, কিন্তু ধারণা করা হয় তিনি ইসলাম ধর্মই বুঝাইছেন।
ওই দ্বীপে দুইজন জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষদের বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন, একজনের নাম সালামান, তিনি নবীদের কাহিনী, ধর্মীয় রীতি নীতি পালনের শিক্ষা দিতে লাগলেন, তিনি ধর্মের বহিঃস্থ দিকে ফোকাস করতেন। এবং আরেকজন লোক, আবসাল, তার মত ছিল ধর্মের এই ব্যাখ্যা দিয়ে কাজ হবে না। ধর্মের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা মানুষরে দিতে হবে। এই মত বিরোধের এক পর্যায়ে আবসাল ওই দ্বীপ ত্যাগ করেন একা সাধনার জন্য।
আবসাল চলে আসেন হাই এর দ্বীপে, নির্জনে সাধনা করার জন্য। হাই এর সাথে যখন তার দেখা হয় - হাই একা একা বড় হওয়া একজন মানুষ যে আগে মানুষই দেখে নি। প্রাথমিক ভাবে তাদের অসুবিধা হয় যোগাযোগে। কিন্তু এই বাঁধা কাটিয়ে উঠলে আবসাল দেখতে পান হাই অনেক জ্ঞানী, তিনি ধর্ম থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা হাই একা একাই অর্জন করে ফেলেছে। অন্যদিকে হাই দেখতে পায় আবসাল যে বিশ্বাসের কথা বলছেন, ওই বিশ্বাসই তার আছে, ফলে সে ওই ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারা দুইজন ঠিক করেন দ্বীপে ফিরে গিয়ে মানুষদের মাঝে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বানী প্রচার করবেন।
তারা দ্বীপে যান, ধর্মের প্রকৃত বানী প্রচার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেখতে পান সমাজের সবচাইতে জ্ঞানী লোকেরাও তাদের বুঝতে পারছে না। তখন হাই মনে করে, সাধারণ মানুষেরা মূর্খ, এদের জন্য তাই রূপক, প্রথা, রীতিই প্রযোজ্য, এরা প্রকৃত জ্ঞান বুঝবে না।
তখন তারা ব্যথিত হয়ে দুইজন আবার হাই এর দ্বীপে ফিরে আসেন, একা একা জনমানব থেকে দূরে বসে জ্ঞান সাধনা করার জন্য।
এই হলো ইবনে তুফায়েলের পুরোদস্তুর এক দার্শনিক উপন্যাস, হাই ইবনে ইয়াকদান।
তার এই উপন্যাসটি কুরআন এবং আরব্য রজনীর পর সবচাইতে বেশী অনূদিত আরব উপন্যাস হিশেবে খ্যাত। ইউরোপিয়ান এনলাইটনমেন্টের থিংকারদের এই উপন্যাস প্রভাবিত করেছিল, কারণ এর কন্টেন্ট এর স্পিরিট- স্বশিক্ষিত দার্শনিক - এনলাইটনমেন্টের মর্মরে ধারণ করে। একজন মানুষ একা একা বাস করে, একা একা অনুসন্ধান ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে শিখে, স্বশিক্ষিত দার্শনিক হয়ে সৃষ্টিকর্তারেও বুঝে ফেলে - ওই সময়ে এটা এক প্রগ্রেসিভ কাজ, ইন্ডিভিজুয়ালিজম বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এর বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিভূমি তৈরি করে দেয়।
দার্শনিক জন লকের তাবুলা রাসা তত্ত্ব, যে মানুষ জন্ম নেয় খোলা খাতার মত, সে অনুসন্ধান করে, চারপাশ দেখে এমন নিরীক্ষণের মাধ্যমেই বুদ্ধিদীপ্ত হয়। এই তাবুলা রাসাই হাই ইবনে ইয়াকজানে দেখিয়েছেন ইবনে তোফায়েল, কনসেপ্ট হিশাবে এটি এরিস্টটলের মধ্যে ছিল, বিস্তারিত করেন ইবনে সিনা।
ড্যানিয়েল ডিফোর বিখ্যাত গল্প রবিনসন ক্রুসো অনেকে পড়ে থাকবেন, যেখানে জাহাজডুবিতে পড়ে এক নির্জন দ্বীপে একা একা থাকতো রবিনসন ক্রুসো। তার একা বাসের গল্প, দ্বীপের আতঙ্ক মানুষখেকোরা এবং পরে সে একজন বন্য মানুষকে পায়, যার নাম দেয় ফ্রাইডে। এই গল্পের লেখক ড্যানিয়েল ডিফো ইংরাজি অনুবাদে হাই ইবনে ইয়াকজান পড়েছিলেন, এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।
দ্বীপে একা বাস, বা একা জঙ্গলে-দ্বীপে কোন শিশুর বেড়ে উঠা বিষয়ক গল্প উপন্যাসের মূল ধরা যায় হাই ইবনে ইয়াকজানকে, এটা তার সাহিত্যিক ইনফ্লুয়েন্স বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে।
দার্শনিক ভাবে, ইবনে তোফায়েল নতুন কিছু বলেন নি, তিনি ইবনে সিনা, এরিস্টটল, ইমাম গাঁজালি, এবং নির্জনে জ্ঞান সাধনার দিকটাতে ইবনে বাজাহরও অনুপ্রেরণা নিয়েছেন, যদিও তিনি ইবনে বাজাহর কড়া বিরোধী ছিলেন নানা তর্কে। ওই সময়ে ইবনে বাজাহ আরেকজন এরিস্টটলিয়ান দার্শনিক ছিলেন আন্দালুসিয়ায়, তিনি ইবনে তোফায়েল থেকে বয়েসে বড় ছিলেন কিন্তু কখনোই ইবনে তোফায়েলের শিক্ষক ছিলেন না, যেটা ভুলভাবে কেউ কেউ বলে থাকেন। এরিস্টটলিয়ান সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব এবং এরিস্টটল বিষয়ক কিছু ব্যাখ্যা ও অনুমানে ইবনে বাজাহর সাথে তোফায়েলের বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধ ছিল। এর প্রধান জায়গা, ইবনে তোফায়েল মনে করতেন মানুষ সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত হতে মিস্টিক, আধ্যাত্মিক পর্যায়ে যেতে হয়, যেটা তিনি তার হাই ইবনে ইয়াকজানে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে ইবনে বাজাহ মনে করতেন মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ডেভলাপমেন্টের মধ্য দিয়েই সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত হতে পারে, তিনি ইমাজিনারি বা আধ্যাত্মিকরে অস্বীকার করতেন এখানে। দর্শনে কল্পণা এবং ইনটুইশনরে অস্বীকার করায় তোফায়েল ইবনে বাজাহর সমালোচনা করতেন। কিন্তু এটাও স্বীকার করতেন ওই সময়ের একজন প্রখর চিন্তক ইবনে বাজাহ।
এরিস্টটল দার্শনিক হিশাবে তার গুরু প্লেটোর বিরুদ্ধে গিয়ে দর্শন, আধ্যাত্ম্য ও অধিবিদ্যা বিরোধী ছিলেন। যেটা রাফায়েলের আঁকা ফ্রেস্কোতে তাদের দুইজনের ছবির উপস্থাপনেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।প্লেটো যেখানে আঙ্গুল উপরে দিয়ে তার অধিবিদ্যা বা ভাববাদী অবস্থান দেখাচ্ছেন, সেখানে এরিস্টটল হাত নিচের দিকে করে বাস্তবে দৃষ্টি দিতে বলছেন।
ইবনে তোফায়েলের এরিস্টটল বুঝার সাথে যুক্ত হয়েছিল আল গাঁজালির সূফীবাদী চিন্তা, তিনি ধর্ম ও দর্শনের এক সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন ধারনা করা যায়। ইবনে তোফায়েলের ছাত্র ছিলেন সবচাইতে বড় একজন এরিস্টটলিয়ান, ইবনে রুশদ। তারে বলা হইত দি কমেন্টেটর (আর দি ফিলোসফার বলতে একজনরেই বুঝানো হইত তখন, এরিস্টটল), কারণ তিনি এরিস্টটলের কাজের উপর কমেন্টারি লিখেছিলেন। এই কাজ তাকে করতে বলেছিলেন তার গুরু ইবনে তোফায়েল। তোফায়েল একদিন তারে ডেকে নিয়ে বলেন, এরিস্টটলের কাজ বুঝা কঠিন। এগুলা পড়ে ব্যাখ্যা, সারমর্ম লেখা দরকার। আমার বয়েস হয়েছে এবং রাজনৈতিক দায়িত্বও অনেক। তা না হলে আমিই এই কাজ করতাম। তোমার জ্ঞান সাধনা, অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম সম্পর্কে আমি জানি, আমার মনে হয় তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করা উচিৎ।
ইবনে রুশদকে নিয়ে একটা ফিল্ম আছে, ডেস্টিনি নামে, ১৯৯৭ সালে মিশর-ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়।
উপস্থাপনের নতুনত্বে, আইডিগুলার সম্মিলনে ইবনে তোফায়েল এক দার্শনিক রূপগল্পের ব্যাখ্যা দেন হাই ইবনে ইয়াকজান উপন্যাসটাতে, এইজন্য এর দার্শনিক গুরুত্ব ব্যাপক হয়েছিল, এবং এখনো দার্শনিক উপন্যাসের সারিতে এর স্থান প্রথমদিকে। এটিকে ধরা হয় প্রথম দার্শনিক উপন্যাস, এবং বর্তমান এই আধুনিক যুগের হিউম্যানিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কেন্দ্রিক অনেক ধারণা তৈরির পেছনে এর অবদান অনেক।
হাই ইবনে ইয়াকজান ফিলোসফাস অটোডিডাক্টাস নামে ল্যাটিন ভাষা নামকৃত হয়, ইংরাজিতে আক্ষরিক অর্থ করলে হয়, ‘এলাইভ, সান অব এওয়াক', এটারে বাংলা করলে, বাংলার টোনে হবে, জাগ্রতের জীবিত সন্তান।